প্রতি ১০ জন মার্কিন নাগরিকের একজন টেলিভিশনের তথ্যে বিশ্বাস করে আর প্রতি ৬ জনের এক জন সংবাদপত্রে বিশ্বাসী বলে গ্যালাপের সর্বশেষ (২০২২) জরিপে উঠে এসেছে। গ্যালাপ এটাকে বলছে 'মিডিয়া কনফিডেন্স রেটিংস' (Media Confidence Ratings)।
১৯৭৩ সালের পর নিউজমিডিয়ার ওপর আমেরিকার মানুষের 'ঈমানের' ঘাটতি এতোটা প্রকট দেখা যায়নি৷
জরিপ থেকে দেখা যায়, মাত্র ১৬% মার্কিন জনগণ সংবাদপত্রে বিশ্বাস রাখছে আর এর চেয়ে ঢের কম ১১% মানুষ টেলিভিশন সংবাদে বিশ্বাস করে। গ্যালাপ এ বিশ্বাসকে বলছে 'Degree of Confidence' এবং প্রশ্নে থাকা ''Great Deal/quite a lot of confidence"কে আস্থা বা বিশ্বাস হিসেবে পাঠ করেছে।
জরিপ/গবেষণার প্রশ্নে বা গবেষণা/জরিপের ফল উপস্থাপনের নানা ফাঁকফোকর, ধান্ধা থাকলেও মার্কিন জনগণের গণমাধ্যমের ওপর আস্থা কমে যাওয়ার যৌক্তিকতার প্রমাণ রয়েছে৷ পার্লার (Parler) ও এইটচ্যান বা ফোর চ্যানের (8/4Chan) জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার এটাই কারণ৷ গ্যালাপ বলছে, এখনো যতটুকু বিশ্বাস মিডিয়ার প্রতি আছে তার অধিক করে ডেমোক্রেটরা। মূলধারার মিডিয়ার প্রতি রিপাবলিক ও স্বাধীন মতের মানুষের আস্থা আরো ক্রমহ্রাসমান।
বাংলাদেশের মিডিয়ার প্রতি কেমন আস্থা লোকের এটি নিয়ে গবেষণা করার মত লোকও এদেশে নাই, আর এটি কেউ করলেও আমাদের মিডিয়ার লোকদের তা প্রকাশের হিম্মত নেই।
সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষা, সংখ্যা ৩ (আদনান ও মঈনুল, ২০১৮) তে প্রকাশিত আমার ও আদনান স্যারের করা একটি গবেষণায় উঠে এসেছিল যে, বাংলাদেশের মানুষ সংবাদ ও তথ্যপ্রাপ্তির মূল উৎস হিসেবে ব্যবহার করছে মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে।
আবার, এই মাধ্যমেই আবার অনেকে নয়া মতে দীক্ষিত হচ্ছে। অনেকে এখানে মতস্রষ্টাও হচ্ছেন। অর্থাৎ মত মোড়ল যেভাবে মিডিয়ার তথ্যকে নিজের মত করে তাফসির ও প্রচার করে এখানে হুবহু তা হয় না। এখানে, মতস্রষ্টা একেবারে নিজের মতকেই প্রচার শুরু করে দেয়। ফেসবুক হয়েছে প্রত্যেকের পারসোনাল মাস মিডিয়া।
বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মিডিয়ার প্রতি অনাস্থা বাড়ছে। কথিত শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অল্প, অর্ধ শিক্ষিত বা নিরক্ষরদের মূলধারার মিডিয়ার ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্থা কম, এটা আমার অভিজ্ঞতা৷
কথিত শিক্ষিতদের মধ্যে আবার মার্শাল ম্যাকলুহানের (১৯৬৪) 'মাধ্যমকেই বার্তা' মনে করাদের সংখ্যা বেশ আছে। যেমন, একটি অডিয়েন্সগোষ্ঠী আছে যাদের নিকট 'প্রথম আলো বা ডেইলি স্টার হচ্ছে আসমানী কিতাবের মত বিশুদ্ধ'। এর বাইরের তথ্য তারা সন্দেহের চোখে দেখেন কেবল তা নয়, যেকোনো তথ্য বা সংবাদকে প্রথম আলো-ডেইলি স্টারের ছাঁকনিতে পরিমাপ করেন।
অন্যদিকে, বাংলাদেশের মিডিয়ার মালিকানা বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের হাতে৷ এ ব্যবসায়ীরা আবার কোনো না কোনভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী (অধিকাংশ মিডিয়া ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শকেই ধারণ করে)।
এডওয়ার্ড এস হারম্যান ও নোয়াম চমস্কির বর্ণিত (১৯৮৮) 'অপপ্রচার নকশা' (Propaganda Model) এর সবচেয়ে শক্তিশালী ছাঁচ 'মালিকানা'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চমস্কির এই ৫ ছাঁচ আসলে একই রূপের ৫ টি শাখা। 'টাকা' ও 'ক্ষমতা' এখানে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করে। আবার, যার টাকা আছে সেই টাকা সুরক্ষায় বা আরো টাকা বানাতে তার দুটি জিনিসের প্রয়োজন হয়।
১। পয়সা উপার্জন সহজীকরণ ও পয়সার প্রবাহ সচল রাখার জন্য ক্ষমতা
২। পয়সা পাহারা দেওয়ার জন্য, বা পয়সা উপার্জনের প্রতিবন্ধকতা যেমন--আইন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রতিপক্ষ ইত্যাদিকে জয় করার জন্য মিডিয়া।
এ কারণে বাংলাদেশে যে 'মালিক' (Ownership), সে আবার 'বিজ্ঞাপনদাতা' (Funding Source) [আনভীর বিজ্ঞাপন দেয় কী না এই ভয়ে মুনিয়া হত্যায় তার পরোক্ষ সংযোজন নিয়ে সংবাদ হয় না]; সেই মালিক আবার 'সংবাদ সূত্রের ওপর প্রভাববলয় তৈরি করতে পারে' (Sourcing) (মুনিয়ার বোন কাকে তথ্য দেয়, কার মাধ্যমে দেয় তা আনভীর জানে। ট্রান্সকম গ্রুপ তাদের যে এন্টারটেইনমেন্ট ও ইন্টেলেকচুয়াল বলয় তৈরি করেছে তারা যদি 'সট/কমেন্ট/এক্সপার্ট সোর্স' হয় তবে তাদের মাধ্যমে ইভেন্ট ম্যানুপুলেশনকে এ ধাঁচে ফেলা যায়?);
একই মালিক আবার তার বাহিনী দিয়ে সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিককে হুমকি দিতে পারে বা মামলা করে হয়রানী করতে পারে, অপছন্দের ফেসবুক পাতা বা ইউটিউব চ্যানেল গায়েব করে দিতে গণরিপোর্টের চেষ্টা চালাতে পারে (Flak) [কালেরকণ্ঠ ও প্রথম আলোর দ্বন্দ্ব দ্রষ্টব্য, ফেসবুক রিপোর্ট তো সবাই জানি];
এবং এই একই মালিক আবার তার গণমাধ্যমের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের সন্তোষে নেই এমন মতকে প্রতিপক্ষ হিসেবে সেট করতে পারে (Anti Communism/Anti Islam/or Such) [এটা শুরু হয় রাজনৈতিক বিশুদ্ধতাবাদী চিন্তা থেকে। এর ইংরেজি নাম Political Correctness]।
অন্যদিকে ম্যাক্স হোরখেইমার আর থিওডর এডর্নোর মতে ''সাংস্কৃতিক বিনোদন কারখানা' (Culture Industry, ১৯৪৭) এই মিডিয়ার মাধ্যমেই গণমানসে সম্মতি বা অসম্মতি উৎপাদন করতে পারে। ক্ষমতাসীনরা যখন নাগরিকের বিনোদন নিয়ে ভাবে বা বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নানা কাজে লাগায় তখন সেই বিনোদন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিরীহ নয়। যেমন, ভারতের প্রপাগাণ্ডা চলচ্চিত্র কাশ্মির ফাইলস, কেরালা, আরআরআর, ফারাজ বা বাংলাদেশের বিভিন্ন কনসার্ট, গানবাংলার মালিকের হাততালি ইত্যাদি। পাশাপাশি, সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের বদলে স্তুতি, টকশোতে একপাক্ষিকতা, খবর বিকৃতি ইত্যাদিতো আছে। সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিনোদনের মাধ্যমে মানে গান, নাচ, মিম, স্পনসরড কনটেন্ট দিয়ে অপপ্রচার তো আছে। এর নাম তারা 'দ্বান্দ্বিক চেরাগায়ন' (Dialectic Enlightenment) দিয়েছিলেন।
একে গ্রামসি 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' (Cultural Hegemony) বলেন। আর গ্রামসির ভাবাদর্শে বিশ্বাসী অলথুসার বলেন 'বুদ্ধিবৃত্তিক রাষ্ট্রযন্ত্র' (Intellectual State Apparatuses)। এগুলোর উৎপাদন ও বণ্টন হয় গণমাধ্যম ব্যবহার করে। আর এই সব কিছুই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।
যাহোক, মানুষের মন থেকে মিডিয়ার প্রতি যে অবিশ্বাস তা দূর করতে পারা ভীষণ জরুরি কাজ হওয়া উচিত। কারণ, 'তথ্যের ঘাটতি'ই কিন্তু মানুষকে অজ্ঞ করে এবং এই অজ্ঞতা ভীতি তৈরি করে। ভীতি থেকে অনিরাপত্তা তৈরি হয় এবং এই অনিরাপত্তা পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা, সংঘাত তৈরি করে। এ জন্যই তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা একটি সভ্য সমাজে সর্বাগ্রে স্থান পায়। এই লক্ষ্যেই বাংলাদেশে ২০০৯ এ জনগণের জানার অধিকার আইন আকারে প্রণীত হয়।
জানতো না, বা মিথ্যা জানতো বলেই ২০০৩ সালের ২০ মার্চ একটি সাজানো দেশ ইরাকে হামলা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এবং মিডিয়ার মিথ্যাচারে অধিকাংশ মার্কিন জনগণ যুদ্ধের পক্ষেই সায় দেয়। সে সময় মিডিয়া মিথ্যাকে সত্য বানিয়েছিল যুদ্ধাপরাধী বুশ-ব্লেয়ার এবং ইহুদি পল উল্ফউইটজ এর কুপ্ররোচনায়। কোথাও Weapons of Mass Destruction নেই! ইরাক যুদ্ধের কনসিকুয়েন্স আজো বিশ্ব টানছে! একটা মিথ্যা কোটি মানুষের জীবন নাশ করলো অথচ নাটের গুরুরা কেউই যুদ্ধাপরাধী বলে মিডিয়ার মাধ্যমে তুলোধুনো হচ্ছে না।
আমার পছন্দের মানুষ জুলিয়ান এসাঞ্জ একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন ২০১৫ তে জার্মানির 'দের স্পিগাল'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ, মিথ্যা প্রকাশের মাধ্যমে যদি যুদ্ধ শুরু হতে পারে, তবে শান্তিও সত্য প্রকাশের মাধ্যমে আসতে পারে৷ ইংরেজিতে বললে কথাটি হয়:
If war can be started by lies, then peace can be regained by the Truth
যদিও সত্যও এখন খণ্ডিত আকারে হাজির হয়। সত্যেরও এখন নানা সংস্করণ। একটা সত্য আছে, নাম উত্তর-সত্য। এর মানে প্রত্যেকে নিজের আবেগ-অনুভূতি ও পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনার নিজস্ব একচোখা সত্য দাঁড় করায়। এর ইংরেজি নাম Post-truth।
আমি বিশ্বাস করি, সত্যের কোনো সংস্করণ থাকা উচিত নয়। সত্যের শাখা প্রশাখা থাকা উচিত নয়। সত্যের একাধিক রূপও থাকা উচিত নয়। সত্যের এজেন্সি থাকবে না। সত্য কেবল সত্য। সবার কাছে একই হবে সত্য।
আর আমি আরও বিশ্বাস করি, সত্যই মুক্তির বুনিয়াদ।

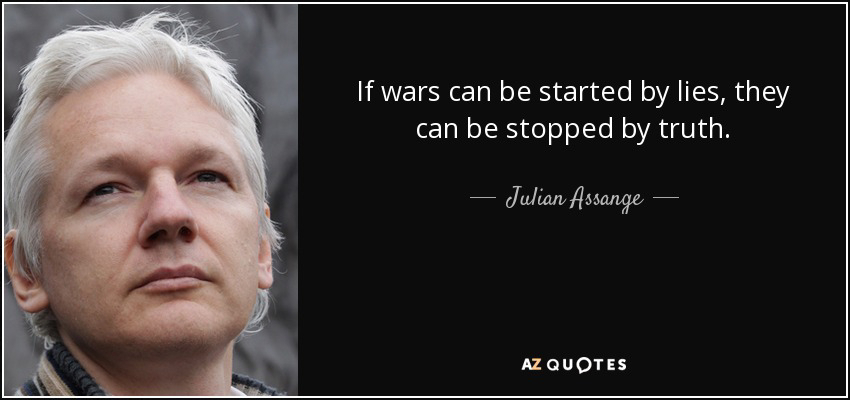





0 Comments